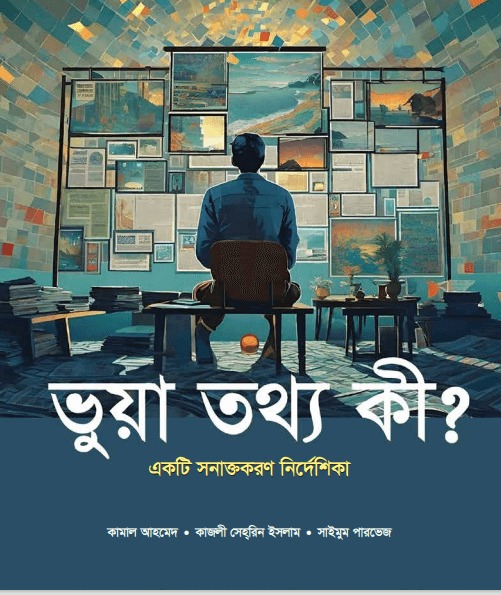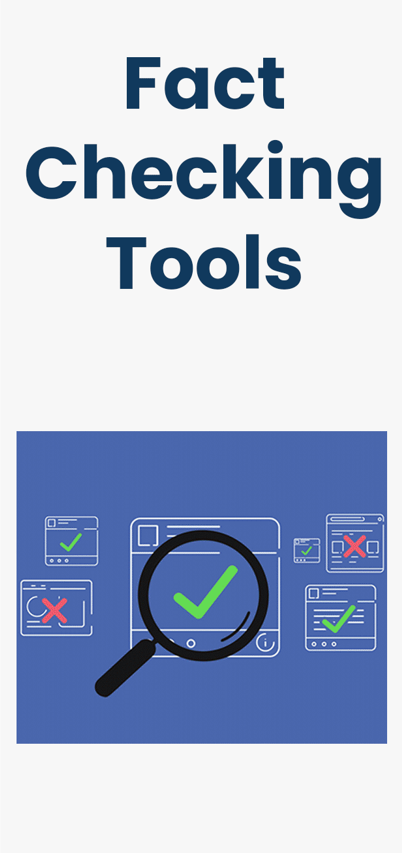আজকে হয়ত ফোনে ঢুকেই দেখলেন ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে, কিংবা সেনাপ্রধানের নামে বিতর্কিত মন্তব্য ছড়িয়ে পড়েছে। মুহূর্তেই চোখে পড়ে এসব খবর। অথচ বাস্তবে কিছুই ঘটেনি। কয়েকশো সমন্বিত অ্যাকাউন্ট কিংবা হাজার হাজার বট একইসাথে কাজ করে মিথ্যাকে এমনভাবে সাজিয়েছে যে সত্যি মনে হয়। আমরা না জেনেই প্রতিদিন এই নাটকের দর্শক হয়ে যাচ্ছি।
অনলাইন দুনিয়ায় এখন ভুয়া তথ্য এক অদ্ভুত বাস্তবতা তৈরি করেছে। বিকৃত ফটোকার্ড, এআই দিয়ে বানানো ভিডিও কিংবা পুরোনো খবরকে নতুন আকারে ছড়িয়ে দেওয়া, সবই আমাদের দৈনন্দিন তথ্যজগতের অংশ। সবচেয়ে ভয়ংকর হলো, এইসব ছড়ানোর পেছনে থাকে সুসংগঠিত ব্রিগেডিং এবং বট বাহিনী।
একবার ভাবুন, আপনি ফেসবুকে একটি পোস্ট দিলেন। হঠাৎ দেখলেন মন্তব্যের বন্যা বইছে, হাজারো মানুষ একই সুরে আপনাকে আক্রমণ করছে। আসলে হয়তো মাত্র কয়েকশো সমন্বিত অ্যাকাউন্ট একসাথে এই কাজ করছে। যারা পড়ছে তারা ভাবে, “এত মানুষ একই কথা বলছে, নিশ্চয়ই সত্য।” এভাবেই ব্রিগেডিং ধীরে ধীরে জনমতকে একপেশে করে দেয়।
বটের কাজ আরও সূক্ষ্ম। এগুলো মানুষের মতো আচরণ করে, কিন্তু আসলে প্রোগ্রামড মেশিন। কয়েক সেকেন্ডে শত শত পোস্ট বা লাইক ছড়িয়ে দিতে পারে। ফলে একটি গুজব মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। সাধারণ ব্যবহারকারীর পক্ষে বোঝা প্রায় অসম্ভব, এটি মানুষের লেখা নাকি মেশিনের তৈরি প্রতিক্রিয়া।
বিদেশে এর ভয়াবহ দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি। ২০১৬ সালের মার্কিন নির্বাচনে লক্ষ লক্ষ ভুয়া অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে রাশিয়ান বট নেটওয়ার্ক গুজব ছড়িয়েছিল। ভারতে নির্বাচনকালে ধর্মীয় উত্তেজনা বাড়াতে বট বাহিনী সক্রিয় ছিল। মিয়ানমারে ফেসবুকের ভুয়া অ্যাকাউন্ট থেকে রোহিঙ্গা বিরোধী প্রচারণা চালানো হয়েছিল, যা সহিংসতাকে উসকে দেয়। এসব উদাহরণ আমাদের শিখিয়েছে, ভুয়া তথ্য শুধু অনলাইনের খেলা নয়, এটি রক্তক্ষয়ী বাস্তবতায় রূপ নিতে পারে।অ্যাক্টিভওয়্যার
বাংলাদেশও এই ঝুঁকি থেকে মুক্ত নয়। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ মাত্র এক মাসে ২৯৬টি ভুয়া তথ্যের ঘটনা নথিভুক্ত করে। এর মধ্যে ৭৫ শতাংশই ছিল রাজনৈতিক। আরও ভয়ের বিষয় হলো, ২৮৯টি ঘটনার উৎস ছিল সোশ্যাল মিডিয়া, সংবাদপোর্টালের অবদান ছিল মাত্র ৭টি। সবচেয়ে বেশি আক্রমণের শিকার হয়েছেন রাজনৈতিক ব্যক্তি ও দল, কিন্তু আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও ছাড় পায়নি।
একটি ঘটনায় দেখা যায়, সেনাপ্রধান নাকি সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কটূক্তি করেছেন, এমন একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওটিতে ইউনিফর্ম, লোগো সবই নিখুঁতভাবে সাজানো ছিল, অথচ বাস্তবে এটি পুরোপুরি এআই দিয়ে বানানো। আবার মাইলস্টোন স্কুলে বিমান দুর্ঘটনার পর ফেসবুকে একটি ফটোকার্ড ভাইরাল হয়। সেখানে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেসসচিবের নামে বলা হয়েছিল, বিদেশি শক্তি দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত। অথচ ওই বক্তব্য তিনি কখনোই দেননি। ফটোকার্ডটি তৈরি হয়েছিল দুর্ঘটনার দুই দিন আগেই। এটি ছিল নিখাদ প্রপাগান্ডা।
প্রশ্ন আসতে পারে, এসব অনলাইন গুজব আমার জীবনে কী প্রভাব ফেলতে পারে? বাস্তবে প্রভাব ভয়ংকর। আর্থিক গুজব মানুষকে ব্যাংক থেকে হঠাৎ টাকা তুলতে বাধ্য করতে পারে, যা পুরো অর্থনীতিকে কাঁপিয়ে দেয়। ধর্মীয় গুজব মুহূর্তেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্ম দিতে পারে। রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা নির্বাচনের ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে। এমনকি একজন সাধারণ মানুষও হঠাৎ ভুয়া প্রচারণার শিকার হতে পারেন, যার কারণে তাঁর ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।
তাহলে আমরা কী করব? প্রথমত, প্রত্যেকে নিজের দায়িত্ব নিতে হবে। খবর শেয়ার করার আগে অন্তত দুটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে যাচাই করতে হবে। প্রয়োজনে গুগল রিভার্স ইমেজ সার্চ বা অফিসিয়াল মিডিয়া পেজ দেখে নেওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, আমাদের ডিজিটাল সাক্ষরতা বাড়াতে হবে। তরুণ প্রজন্মকে বোঝাতে হবে কিভাবে ফটোকার্ড বানানো হয়, এআই ভিডিও তৈরি হয়, কিংবা বট অ্যাকাউন্ট কাজ করে।
সংবাদমাধ্যমকে আরও দ্রুত ফ্যাক্ট-চেক প্রকাশ করতে হবে, যাতে গুজব ছড়ানোর আগেই ভুয়া খবর থামানো যায়। সরকারেরও উচিত নীতি ও প্রযুক্তি উভয় দিক থেকে পদক্ষেপ নেওয়া, যাতে বট নেটওয়ার্ক ও সংগঠিত ব্রিগেড ধরা যায়। আর গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সংগঠনগুলোকে নিয়মিত তথ্য যাচাই করে জনগণের সামনে পরিসংখ্যান হাজির করতে হবে।
আমরা যদি আজ মিথ্যার এই জাল চিনে না নিই, তবে কাল হয়তো আমাদের ভবিষ্যৎই এর হাতে বন্দি হয়ে পড়বে। তখন গণতন্ত্র, অর্থনীতি, সমাজ, সবকিছু ভুয়া বাস্তবতার নাট্যমঞ্চে পরিণত হবে। সত্যকে রক্ষা করা মানে কেবল নৈতিক দায়িত্ব নয়; বরং এটি আমাদের নিরাপত্তা, আমাদের সমাজের শান্তি এবং দেশের ভবিষ্যৎ রক্ষার লড়াই। প্রশ্ন হলো, আপনি কি সত্যকে রক্ষা করার এই লড়াইয়ে অংশ নিতে প্রস্তুত?
লেখক: আপন জহির
গবেষক, বর্তমানে সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজে কর্মরত।