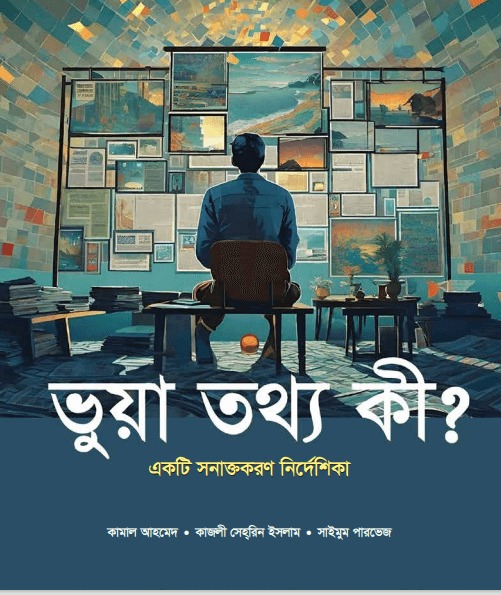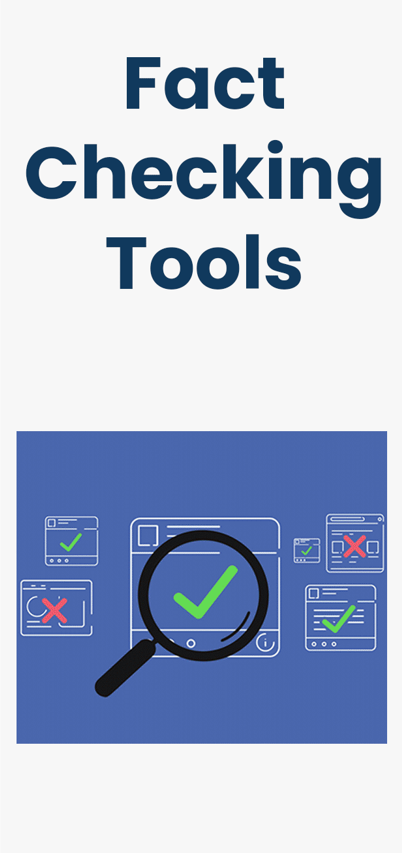ভুয়া তথ্য বা মিথ্যা প্রচারণা আজকের বিশ্বে সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্রগুলোর একটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে এটি ব্যক্তি পর্যায়ে মানুষের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে ব্যবহৃত হচ্ছে, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক দল বা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলো এটি ব্যবহার করছে প্রতিপক্ষকে দুর্বল করার হাতিয়ার হিসেবে। এই ধরনের তথ্যের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে রাজনীতি। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে ভুয়া তথ্য ছড়ানো যেন এক প্রাত্যহিক বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। জুলাই বিপ্লবের পর দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে ক্ষমতার শূন্যতা তৈরি হয়েছে, সেটি ভরাট করতে এখন প্রতিটি দলই—তা তারা শাসকদলের বিরোধী হোক কিংবা পূর্বে দমন-নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকুক—ভুয়া তথ্যের আশ্রয় নিচ্ছে। পরিণতিতে বাংলাদেশে ভুয়া তথ্য একটি বড় সামাজিক-রাজনৈতিক হুমকিতে রূপ নিয়েছে।
২০২৫ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে কেন্দ্র করে একটি ভুয়া তথ্য ভাইরাল হয়। ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া একটি স্ক্রিনশটে দাবি করা হয় যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ড. ইউনূস কর ফাঁকি দিয়েছেন ১১ বিলিয়ন টাকা। স্ক্রিনশটে তারিখ দেখানো হয় ১৭ আগস্ট ২০২৫, এবং শিরোনাম ছিল “ড. ইউনূস কর ফাঁকি দিয়েছেন ১১ বিলিয়ন টাকা: এনবিআর”। প্রথম দেখায় মনে হয়, ড. ইউনূস তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার পরপরই এ খবর প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল পুরোনো একটি খবর, যেখানে মূল প্রকাশের তারিখ ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয়, যাতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়। এই ঘটনাই প্রমাণ করে কীভাবে ভুয়া তথ্য কৌশলে তৈরি হয় এবং তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।
ভুয়া তথ্য থেকে ডাকসু নির্বাচন-ও রেহাই পায়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন হয় ২০২৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর। নির্বাচনের আগেই ভুয়া তথ্যের জোয়ার বইতে শুরু করে। প্রার্থীদের নিয়ে বিভিন্নভাবে ট্যাগ করা, শারীরিক বিদ্রূপ, গুজব ছড়ানো, আক্রমণাত্মক মন্তব্য, ঘৃণামূলক বক্তব্য ও ভ্রান্ত প্রচার চালানো হয়। বিশেষ করে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঘোষিত প্যানেলকে ঘিরে ব্যাপক ভুয়া তথ্য প্রচারিত হয়। তাদের প্যানেলে ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) পদে ছিলেন আবু সাদিক কায়েম এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ছিলেন এস. এম. ফরহাদ। কিন্তু মনোনয়ন ঘোষণার পরপরই তাদের বিরুদ্ধে ভুয়া প্রতিবাদলিপি ছাত্রলীগের প্যাডে ছড়িয়ে দেয়া হয়। তাতে দাবি করা হয় যে, এরা ছাত্রলীগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। যদিও বাস্তবে উভয় প্রার্থীই নিজেদের অবস্থান থেকে ব্যাখ্যা দেন এবং অভিযোগের জবাব দেন। পরবর্তীতে বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই সংগঠনের শিরোনামপত্রগুলো ছিল সম্পূর্ণ জাল, এমনকি তারিখও বিকৃত করা হয়েছিল। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকেও এমন কোনো বিবৃতি প্রকাশিত হয়নি। বরং ছড়ানো প্রতিবাদলিপির বাক্য গঠনে অসংখ্য অসঙ্গতি ছিল, যা ভুয়া হওয়ার প্রমাণ দেয়।
ডাকসু নির্বাচনে আরেকটি বড় ভুয়া তথ্য ছড়ানো হয় বিএনপি-সমর্থিত ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খানকে ঘিরে। দাবি করা হয় যে, তিনি ভিপি নির্বাচিত হয়েছেন। অথচ কোনো স্বীকৃত সংবাদমাধ্যমে ফল প্রকাশের আগেই কালের কণ্ঠের লোগো ব্যবহার করে একটি ভুয়া ফটোকার্ড তৈরি করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই ফটোকার্ডে বলা হয়, ভিপি নির্বাচিত হয়েছেন আবিদুল ইসলাম খান, জিএস হয়েছেন এস. এম. ফরহাদ এবং এজিএস হয়েছেন আবু বকর মজুমদার। পরে কালের কণ্ঠ প্রকাশ্যে জানায়, এ ধরনের খবর তারা প্রকাশ করেনি। এটি নিছক তাদের লোগো ব্যবহার করে বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরির চেষ্টা ছিল।
ডাকসুর মতো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনকেও ঘিরে ভুয়া তথ্য প্রচারিত হয়। ২০২৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনের আগে ফেসবুকে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। সেখানে দাবি করা হয়, ভোট বর্জনের পর শিবির ও ছাত্রদল সংঘর্ষে জড়িয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা যায়, ভিডিওটি আসলে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এর। সেদিন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়কদের উদ্যোগে “গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ” নামে নতুন একটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। সংগঠনের আহ্বায়ক হন আবু বকর মজুমদার এবং সদস্যসচিব হন জাহিদ আহসান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে সংবাদ সম্মেলনের সময় সেখানে দুই দফায় পাল্টাপাল্টি স্লোগান ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। অথচ এই পুরোনো ভিডিওকে নতুন নির্বাচন-সংক্রান্ত সংঘর্ষ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।
একইভাবে ছড়ানো হয় আরেকটি ভুয়া ফটোকার্ড। সেখানে কালের কণ্ঠের নামে দাবি করা হয় যে, শিবির সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জাকসু নির্বাচনে শিবিরকে বিজয়ী ঘোষণা করতে বলেন, নইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে খারাপ পরিণতি ঘটবে। অথচ ১২ সেপ্টেম্বর কালের কণ্ঠে প্রকাশিত ১৫৪টি ফটোকার্ডের মধ্যে এ ধরনের কোনো বক্তব্য ছিল না। তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজেও এমন কিছু পাওয়া যায়নি।
ভুয়া তথ্যের ব্যাপকতা বোঝাতে কিছু পরিসংখ্যান যথেষ্ট। সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস)–এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশে মোট ৩৪০টি ভুয়া তথ্য শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ২৬৮টি ছিল রাজনৈতিক। বাকি ভুয়া তথ্যগুলোর মধ্যে ধর্মীয় ও বিনোদন-সংক্রান্ত ১৬টি, অনলাইন গুজব ১৩টি, কূটনৈতিক বিষয়ে ১১টি, পরিবেশ-সংক্রান্ত ৯টি, অর্থনৈতিক ৫টি এবং সাম্প্রদায়িক বিষয়ে ২টি। অর্থাৎ ভুয়া তথ্যের মূল লক্ষ্যবস্তু রাজনীতি হলেও অন্য ক্ষেত্রও বাদ যাচ্ছে না।
ভুয়া তথ্য শুধু দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নয়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ককেও প্রভাবিত করছে। জুলাই বিপ্লবের পর বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক যে সংকটে পড়েছিল, সেখানে নতুন করে আগুনে ঘি ঢালে “ভারতে বাংলাদেশি রোগীদের নির্যাতন” শিরোনামের একটি ভিডিও। ভিডিওতে দেখা যায়, হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী বাংলাদেশি রোগী ও তাদের আত্মীয়দের হয়রানি করছে। কিন্তু পরে জানা যায়, এটি আসলে ২০২৫ সালের ১২ এপ্রিল পাঞ্জাবে ঘটে যাওয়া একটি পুরোনো ঘটনা, যা হিন্দুস্তান টাইমস-ও প্রকাশ করা হয়েছিলো। একই ভিডিও আগে অন্য সময়ও ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং তখনও এটি ভুয়া প্রমাণিত হয়।
আন্তর্জাতিক পরিসরে একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ট্যামি ব্রুসের নাম ব্যবহার করে দাবি করা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্র চায় আওয়ামী লীগ আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহন করুক। আবার সাবেক মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলারের একটি পুরোনো ভিডিও দেখিয়ে বলা হয়, শেখ হাসিনার পদত্যাগ আন্তর্জাতিক আইনে অবৈধ এবং ড. ইউনূস সরকারকে ক্ষমতা হস্তান্তরের নোটিশ পাঠানো হয়েছে। বাস্তবে এসব দাবির কোনো সত্যতা নেই। পুরোনো ভিডিওগুলোকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্যবহার করে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করা হয়েছে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করার জন্য।
প্রশ্ন জাগে, মানুষ কেন ভুয়া তথ্য ছড়ায় এবং কেন সহজেই তা বিশ্বাস করে? যদি ভুয়া খবর কেবল ভুল তথ্য হতো, তবে তা যারা বিশ্বাস করে তারা হয়তো অজ্ঞ বা সংবাদ বিষয়ে অমনোযোগী। কিন্তু গবেষক রাসেল ফ্র্যাঙ্ক ভুয়া খবরকে লোকসাহিত্যের একটি ঘরানা হিসেবে দেখেছেন। তার মতে, ভুয়া খবর আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে কারণ এটি একটি নৈতিক বয়ান দেয় বা মানুষের আগে থেকেই থাকা বিশ্বাসকে নিশ্চিত করে। যেমন—আইসিসের পশ্চিমা বিশ্বের দুর্নীতি নিয়ে প্রচারণা কিংবা ২০১৬ সালের মার্কিন নির্বাচনে হিলারি ক্লিনটনের স্বাস্থ্যের বিষয়ে ভুয়া তথ্য—সবই মানুষের বিদ্যমান বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছে। ফলস্বরূপ সাধারণ মানুষ সংবাদটি যাচাই করার প্রয়োজন বোধ করে না; বরং অনায়াসে সেটিকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করে।
ভুয়া তথ্য মোকাবিলায় শুধুমাত্র সরকারের আইন প্রণয়ন যথেষ্ট নয়। প্রথমত, জনগণকে সচেতন হতে হবে। যাচাই না করে কোনো তথ্য শেয়ার করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, যুব সমাজ, সাংবাদিক, সামাজিক কর্মী, নারী ও সংখ্যালঘু অধিকারকর্মী, লেখক, ব্লগার, চলচ্চিত্র নির্মাতা, আলোকচিত্রী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। তৃতীয়ত, মূলধারার গণমাধ্যমের দায়িত্বশীল হতে হবে। বর্তমানে তাদের প্রতি মানুষের আস্থার আবনতি ঘটেছে। পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং ভিউয়ের জন্য খবর প্রচারের কারণে গণমাধ্যম বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। এর ফলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ভুয়া অনলাইন পোর্টালগুলো জায়গা করে নিয়েছে।
সাংবাদিকদের উচিত নৈতিকতা বজায় রেখে সংবাদ যাচাই করে প্রকাশ করা, জনগণকে সচেতন করা এবং দায়িত্বশীলভাবে সংবাদ পরিবেশন করা। সবশেষে, ফ্যাক্ট-চেকিং সংগঠনগুলোকে শক্তিশালী করা অপরিহার্য। তারা যদি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ভুয়া তথ্য চিহ্নিত করে সচেতনতা বাড়াতে পারে, তবে অনেকাংশে সমস্যা মোকাবিলা সম্ভব।
বাংলাদেশে ভুয়া তথ্য এখন কেবল গুজব নয়, বরং রাজনীতি ও সমাজের জন্য গুরুতর হুমকি। এটি ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করছে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া দুর্বল করছে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে জটিল করে তুলছে। তাই জনগণের সচেতনতা, গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতা এবং ফ্যাক্ট-চেকিং উদ্যোগকে শক্তিশালী করা ছাড়া এই সংকট মোকাবিলা সম্ভব নয়। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা এবং ভুয়া তথ্য প্রতিরোধ করা আজ সময়ের সবচেয়ে জরুরি দাবি।
লেখক: চিফ অব স্টাফ, সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস)
Op-ed Courtesy:
তথ্যের অপব্যবহার: সমাজ ও রাজনীতির ভয়াবহ বাস্তবতা