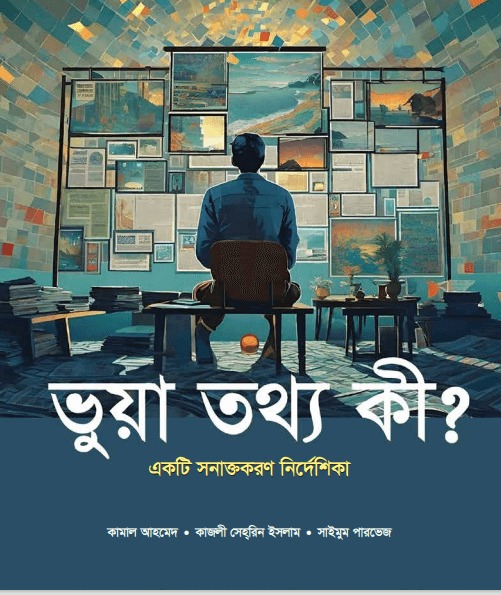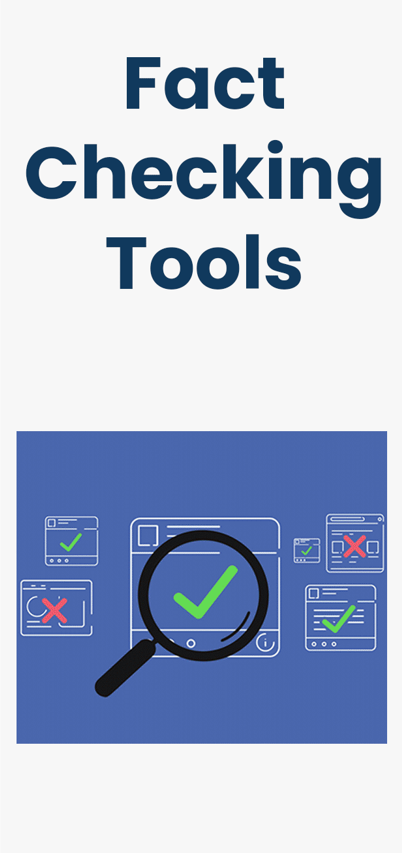রোমান উদ্দিন
এক জেলে ভোরবেলা নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিল। তার জালে প্রতিবারই ভিন্ন ভিন্ন কিছু ধরা পড়ে—কখনো মাছ, কখনো বোতল, কখনো পুরনো কাঁথা। একদিন জালে উঠল একটি সোনালি রঙের বাক্স। গ্রামের সবাই এসে দেখে বিস্মিত, কেউ বলল এর ভেতরে গুপ্তধন আছে, কেউ বলল জ্বীন বাস করে। বাক্স না খোলার পরামর্শ এলো একপাশ থেকে, আবার অন্যপাশ থেকে শুরু হলো উল্টো দাবি। ততক্ষণে, জেলের ঘরে ভিড়, উত্তেজনা আর গুজবের বন্যা। শেষে দেখা গেল, বাক্সটি ছিল একটি নাট্যদলের পুরনো সাজসজ্জার অংশ।
এই গল্পটা গল্পই নয়। এটি আমাদের সময়ের প্রতিচ্ছবি। একটি বিভ্রান্তিকর ছবি, একটি ভিডিও ক্লিপ, কিংবা একটি বিকৃত উদ্ধৃতি, সেটিই এখন সমাজে আলোড়ন তোলে। কে বলেছে, কোথা থেকে এসেছে, সত্য কিনা এসব প্রশ্ন আজ আর কেউ করে না। বিশ্বজুড়ে ভুয়া তথ্য, গুজব, অপপ্রচার এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে তা গণতান্ত্রিক চর্চাকে শুধু বিঘ্নিতই করছে না, বরং রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতার জন্যও হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।
বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক মেরুকরণ, প্রযুক্তির অপব্যবহার এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা হ্রাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভুয়া তথ্য, অপপ্রচার এবং গুজবের বিস্তার ঘটেছে উদ্বেগজনক হারে। আফ্রিকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে শুরু করে ইউরোপের ষড়যন্ত্র তত্ত্বের ব্লগ, দক্ষিণ এশিয়ার ইউটিউব লাইভ থেকে শুরু করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন—সব জায়গায় সত্য আর মিথ্যার দৌড় প্রতিযোগিতা চলছে। বাংলাদেশও এই দৌড়ে পিছিয়ে নেই।
বাংলাদেশে এই সংকট দীর্ঘদিনের, তবে ২০২৪ সালের পর রাজনৈতিক মোড় ঘুরতেই তথ্যের যুদ্ধ যেন নতুন মাত্রা পেয়েছে। গণঅভ্যুত্থান, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উত্থান, শেখ হাসিনার ১৫ বছরের দীর্ঘ শাসনের পতন, আর জনগণের বিভক্ত আবেগ—সব মিলিয়ে ভুল তথ্য ছড়ানোর একটি উর্বর ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। গড়ে উঠেছে ভুল তথ্যের একটি শক্তিশালী ইকোসিস্টেম। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পর্দার আড়ালে থেকে নানা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত গোষ্ঠী এই ভুল তথ্যের বিস্তার ঘটাচ্ছে। এপ্রিল ২০২৫ ছিল সেই ইকোসিস্টেমের একটি স্পষ্ট প্রতিবিম্ব যেখানে ভুয়া ছবি, এআই-জেনারেটেড ভিডিও, কৃত্রিম অডিও ক্লিপ আর পুরনো ভিডিওকে নতুন করে সাজিয়ে গুজব ছড়ানো হয়েছে অভূতপূর্ব হারে।
এই সময়ে বেশ কিছু ভুল তথ্য রাজনৈতিক চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। সবচেয়ে আলোচিত মিথ্যাচার ছিল ড. ইউনূসকে ঘিরে। তাঁর পদত্যাগের ভুয়া ঘোষণা সহ এআই প্রযুক্তিতে তৈরি একটি ডিপফেক ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। এই ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, “আমি আর দায়িত্বে থাকতে চাই না”। অথচ প্রকৃতপক্ষে, এমন কোনো বক্তব্য বা ঘোষণাই তিনি দেননি। একই সময় ভারতের একটি সংবাদমাধ্যমে তাঁর একটি করমর্দনের ছবি প্রকাশিত হয় যেখানে বলা হয়, তিনি পাকিস্তানের এক সেনা কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করেছেন। মূলত সেটি ছিল বাংলাদেশের পুলিশ সপ্তাহের একটি ছবি। এতে করে তাঁর জাতীয়তা এবং নিরপেক্ষতা নিয়ে জনমনে সন্দেহ ও বিভ্রান্তি তৈরি করা হয়।
এই রকম পরিকল্পিত মিথ্যাচার চালানো হয়েছে অন্য রাজনৈতিক নেতার ক্ষেত্রেও। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নামে তৈরি করা হয় একাধিক ফটোকার্ড, যাতে বলা হয়, "ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন না দিলে আন্দোলন হবে।" এসব ফটোকার্ডে টেলিভিশন চ্যানেলের লোগো ব্যবহার করে বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানো হয়। এ ধরনের তথ্য কেবল একটি রাজনৈতিক ব্যক্তিকে হেয় করতেই নয়, বরং জনমনে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে রাজনৈতিক মেরুকরণকে উস্কে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।
মিথ্যা তথ্য সীমান্ত পেরিয়ে আন্তর্জাতিক বিষয়েও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন গাজার একটি বোমা হামলার ভিডিওকে “অপারেশন সিন্দুর” নাম দিয়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের রূপে চালানো হয়। ইন্দোনেশিয়ার একটি ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগার ভিডিওকে ভারতের বিমানঘাঁটির হামলা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এমনকি মিয়ানমারের সংঘর্ষের ভিডিওকে সীমান্ত সংঘর্ষ বলা হয়। এসব ভিডিওর কোনো বাস্তব ভিত্তি ছিল না।
দেশের অভ্যন্তরেও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো হয়েছে। খিলগাঁওয়ের একটি স’মিলের আগুনের ভিডিওকে ভারতীয় হামলা হিসেবে চালানো হয়। একজন আহত ব্যক্তিকে মৃত বলা হয়, বলা হয় সে ট্রেন থেকে পড়ে মারা গেছে, আবার কেউ দাবি করে সে ‘মোবাইল চোর’।
ধর্মীয় ও জাতিগত বিভাজন তৈরির জন্যও ভুয়া তথ্য ব্যবহার হয়েছে। বান্দরবানের এক মারমা কিশোরীর অপহরণের ঘটনা তুলে ধরে বলা হয় বার্মা সেনারা তাঁকে তুলে নিয়ে গেছে। পরবর্তীতে জানা যায়, এসব ছড়িয়েছেন এক ব্যক্তি যিনি নিজেকে নারী ও পাহাড়ি পরিচয়ে ছদ্মবেশী প্রোফাইল বানিয়েছিলেন। একইভাবে পুরোনো ধর্মান্তর সংক্রান্ত একটি হলফনামার ছবি নতুন করে ভাইরাল করা হয়, বলা হয় পরিবারটি চাপের মুখে ধর্ম পরিবর্তন করেছে। এসব তথ্য যাচাই না করে ভাইরাল হওয়ার পর সমাজে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়েছে।
গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস)-এর গবেষণায় দেখা গেছে, এপ্রিল ২০২৫ মাসে দেশে মোট ৩১৩টি ভুয়া তথ্য শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়ক ভুয়া তথ্য ছিল ১৯৬টি, ধর্মীয় বিষয়ে ৪৪টি, বিনোদন খাতে ২৪টি, অর্থনৈতিক বিভ্রান্তি ১৬টি, অনলাইন হোক্স ২০টি এবং কূটনৈতিক বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছিল ১৩টি। টার্গেট বিশ্লেষণে দেখা যায়, রাজনৈতিক ব্যক্তি ও নেতাদের নিয়ে ১০২টি ভুয়া তথ্য ছড়ানো হয়েছে, ধর্মীয় বিষয়কে ঘিরে ৪৫টি, আইনশৃঙ্খলা ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিরুদ্ধে ৩৭টি, সেলিব্রিটি ও রাজনৈতিক দলকে ২৩টি করে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে ১৮টি এবং অন্যান্য সংস্থা ও ধর্মীয় নেতাকে ঘিরে বাকি তথ্যগুলো ছড়ানো হয়েছে। ৫৩টি ভুয়া তথ্য ছিল অনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুকে ঘিরে।
সোশ্যাল মিডিয়া ছিল ভুয়া তথ্য ছড়ানোর প্রধান মাধ্যম। মোট ৩১১টি ভুয়া তথ্য সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো হয়েছে এবং মাত্র ২টি ঘটনা অনলাইন নিউজ পোর্টালের মাধ্যমে।
এই তথ্যগুলো থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, তথ্য এখন একটি রাজনৈতিক অস্ত্র। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা হ্রাস, সোশ্যাল মিডিয়ার লাগামহীনতা এবং জনসচেতনতার অভাব এই অস্ত্রকে আরও বেশি কার্যকর করে তুলেছে।
এসব গুজবকে বোঝার জন্য এবং বিশ্লেষণ করার জন্য একাডেমিক পরিভাষার মধ্যে 'ইনফরমেশন ডিজঅর্ডার' বা 'তথ্য বিশৃঙ্খলা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এই ধারণা অনুযায়ী মিসইনফরমেশন (অজ্ঞতাবশত ভুল তথ্য), ডিসইনফরমেশন (উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভুল তথ্য) এবং ম্যালইনফরমেশন (সঠিক তথ্যের অপপ্রয়োগ) মিলেই তৈরি করে তথ্য বিশৃঙ্খলার চক্র।
তথ্য ছড়ানোর এই পরিবেশকে বোঝাতে আরও একটি তাত্ত্বিক কাঠামো হলো 'মাধ্যম পরিবেশ তত্ত্ব'। এটি বলে, কোনো তথ্য কীভাবে ছড়ায় তা নির্ভর করে কোন মাধ্যমে তা প্রচার হচ্ছে, কীভাবে প্রযুক্তি তা পরিবেশন করছে, এবং সেই প্রক্রিয়ায় মানুষের আচরণ কেমন হচ্ছে। বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যালগরিদম যেসব বিষয় বেশি ভাইরাল করে, তার মধ্যে রয়েছে আবেগ, ক্ষোভ, সন্দেহ এবং ভয়। ভুল তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা এবং তা ছড়িয়ে পড়ার গতি—দুই-ই এই নতুন প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থায় অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ভুয়া তথ্য সহজেই নজরে পড়ে, আর সত্য চাপা পড়ে যায়।
তথ্য বিশ্লেষণ এবং গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বিষয় আরও স্পষ্ট—ভুয়া তথ্য এখন আর নিছক কোনো 'ফেসবুক সমস্যা' নয়। এটি রাজনৈতিক কৌশল, বিদেশি প্রভাব, তথ্য-সন্ত্রাস এবং প্রযুক্তির অপব্যবহারের সম্মিলিত রূপ। কাজেই এর প্রতিকারে কেবলমাত্র ফ্যাক্টচেকিং নয়, প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতিনির্ধারণ, মিডিয়া সাক্ষরতা, প্রযুক্তির জবাবদিহিতা এবং জনসম্পৃক্ততা।
সাংস্কৃতিকভাবেও আমাদের ভাবতে হবে—আমরা কোন তথ্য বিশ্বাস করছি, কেন করছি, এবং তার সামাজিক প্রভাব কী। ভুল তথ্য এখন আর কেবল ভুল নয়, এটি সামাজিক অনাস্থা, রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্ত এবং বিভেদের বিষবৃক্ষ রোপণের মাধ্যম হয়ে উঠেছে।
এপ্রিল ২০২৫ আমাদের সামনে একটি আয়না ধরে রেখেছে, যেখানে আমরা নিজেদেরই এক বিভ্রান্ত সমাজ হিসেবে দেখতে পাচ্ছি। সেই আয়নায় চেয়ে আমরা যদি শুধরে না নিই, তবে ভবিষ্যৎ কেবল আরও অন্ধকার হয়ে উঠবে।
তথ্য যাচাই শুধু সাংবাদিক বা গবেষকের কাজ নয়, এটি এখন প্রতিটি নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। নিজের মত গঠনের আগে, শেয়ার দেওয়ার আগে, বিশ্বাস করার আগে একবার প্রশ্ন করুন—তথ্যটি কোথা থেকে এসেছে, সেটি সত্য কি না। কারণ একটি ভুল তথ্য কখনো কখনো একটি সমাজকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিতে পারে।
রোমান উদ্দিন
গবেষণা সহযোগী, সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস)
Content Courtesy:
ভুল তথ্যের মহামারিতে এপ্রিল মাসের খতিয়ান