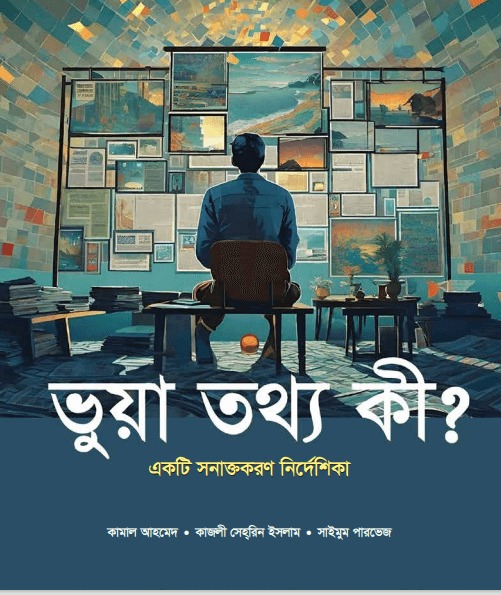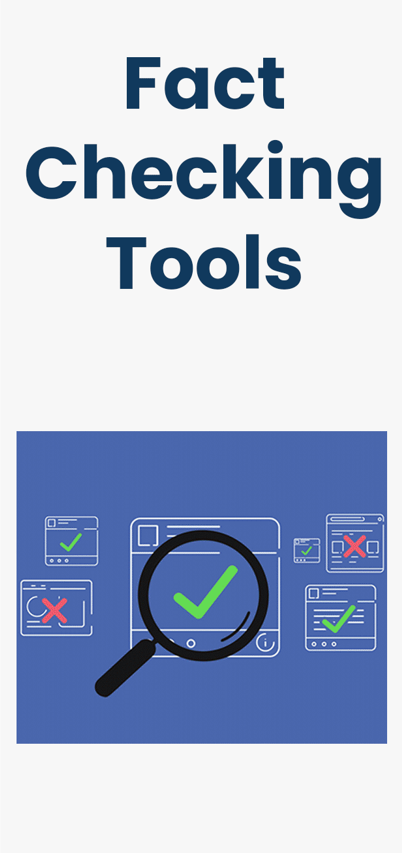শামসুল আরিফ ফাহিম
তথ্যপ্রবাহের স্বাধীনতা বা জনগণের অবাধে তথ্য পাওয়ার অধিকার গণতান্ত্রিক সমাজের মৌলিক স্তম্ভ। যখন অবাধ তথ্যপ্রবাহ সীমিত হয়ে যায়, রাষ্ট্র এবং নাগরিকের সম্পর্কে একটি তথ্যশূন্যতা দেখা দেয়, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় ‘ডেটা ভ্যাকুয়াম’। এই শূন্যতা বা ভ্যাকুয়ামে দ্রুত জায়গা করে নেয় গুজব ও ভুল তথ্য। ঐতিহাসিকভাবেও দেখা গেছে, সরকারি ও নাগরিক সেবার তথ্য লুকানোর প্রবণতা কিংবা সেন্সরশিপ জনগণের মধ্যে সন্দেহ তৈরি করে এবং তারা বিকল্প অনির্ভরযোগ্য উৎসের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সাম্প্রতিক বিশ্বপরিস্থিতিতে যেভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ও অপতথ্যের ছড়াছড়ি দেখা যাচ্ছে, তা অনেকাংশে বিদ্যমান রাষ্ট্রগুলোর তথ্য়প্রবাহে ঘাটতির সুযোগ নিয়েই ঘটছে।
এছাড়া, সরকার কিংবা ক্ষমতাসীনরা শুধুমাত্র তথ্য লুকিয়ে রাখে না, ইচ্ছাকৃতভাবে ভুয়া তথ্য ও মিথ্যা প্রোপাগান্ডাও জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। এটি রাষ্ট্র কর্তৃক নিজ দেশের জনগণের মাঝেই হতে পারে, আবার আন্তঃরাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বেও এর চিত্র দেখা যায়। ভুয়া তথ্য বা প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা নতুন কিছু নয়; এটি শত শত বছর ধরে চলছে এবং নানা সময়ে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে এনেছে। ইতিহাসে একাধিক উদাহরণ রয়েছে, যেখানে অসত্য তথ্য রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় ডেকে এনেছে, যার ফলাফল হিসেবে পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় মানুষদের গণহত্যা ও জেনোসাইডের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। এর প্রকৃষ্ট দুটো উদাহরণ হচ্ছে—(এক) নাৎসি জার্মানির ইহুদিবিদ্বেষী প্রচারণা এবং (দুই) ১৯৯৪ সালের রুয়ান্ডা জেনোসাইড।
হিটলারের নাৎসি সরকার ইহুদিবিরোধী সংগঠিত প্রোপাগান্ডা ব্যবস্থার মাধ্যমে ধারাবাহিক মিথ্যা প্রচার চালায়। তারা ইহুদি জনগোষ্ঠীকে ঘৃণার লক্ষ্যবস্তু বানাতে মধ্যযুগের পুরনো “ব্লাড লাইবেল” (যেখানে বলা হতো, ইহুদিরা খ্রিস্টান শিশুর রক্তপান করে) মিথকে পুনর্জীবিত করে জনগণের অনুভূতিকে উত্তেজিত করে তোলে। এই ধরনের ভুয়া গল্প ও ষড়যন্ত্র তত্ত্ব জার্মান জনমনে ইহুদিবিরোধী বিদ্বেষ উসকে দেয়, যার ফলশ্রুতিতে হোলোকাস্টের মতো মানব ইতিহাসের নৃশংস গণহত্যা সংঘটিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, গোয়েবলসের প্রচারণা মন্ত্রণালয় একচেটিয়াভাবে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত তথ্য সরবরাহ করত। ভিন্নমতের প্রকাশের সুযোগ না থাকায় জনমানসে মিথ্যাই সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং নাৎসি সরকার গণহত্যার পূর্বে ভুয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে জনসমাজে সম্মতি উৎপাদনে সফল হয়, যেটিকে গ্রামসি সংজ্ঞায়ন করেছেন ‘কনসেন্ট হেজিমনি’ হিসেবে— অর্থাৎ, এমন একটি তৎপরতা যা শাসককে ঐতিহাসিক মুহূর্তে জনসমাজের সম্মতি এনে দেয়, যেকোনো বলপ্রয়োগের হস্তক্ষেপ বৈধ করে তোলে। ফলস্বরূপ, ভুল তথ্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ঘৃণা ও বিভ্রান্তি লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ও সামাজিক বিভাজনের জন্ম দেয়।
আরেকটি বড় উদাহরণ হলো ১৯৯৪ সালের রুয়ান্ডা গণহত্যা, যেখানে হুতু কর্তৃত্ববাদী সরকার সংগঠিতভাবে টুটসি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ভুয়া তথ্য ও বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারণা চালিয়েছিল। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত রেডিও “আটিএলএম” টুটসিদেরকে “সাপ” ও “তেলাপোকা” বলে আখ্যায়িত করে, তাদের অমানবিক ও শত্রু হিসেবে চিত্রিত করে। পাশাপাশি সঙ্গীত ও খবরে মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হয় যে, টুটসিদের নির্মূল করাই দেশের জন্য মঙ্গলকর। এক রুয়ান্ডা জেনোসাইড থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি মন্তব্য করেন, “ভুল তথ্য, বিভ্রান্তিকর তথ্য ও প্রোপাগান্ডা সরাসরি ১৯৯০-১৯৯৪ সালের জেনোসাইডের পথ প্রশস্ত করেছিল।” মিথ্যা তথ্যের এই প্রচারণা হুতু জনসাধারণকে টুটসিদের হত্যায় উস্কে দেয় এবং মাত্র ১০০ দিনে প্রায় আট লক্ষ মানুষ নির্মমভাবে নিহত হয়। রুয়ান্ডার দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়—পরিকল্পিতভাবে ছড়ানো অসত্য তথ্য কীভাবে ভয়াবহ সহিংসতা ও সমাজবিধ্বংসী পরিস্থিতির জন্ম দিতে পারে।
এছাড়া, ডিজিটাল রাজনৈতিক পরিসরেও এর বাস্তব রূপ দেখা যায়। ২০১৬ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুয়া খবরে ছেয়ে যায়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, নির্বাচনী প্রচারের শেষ তিন মাসে ফেসবুকে সবচেয়ে জনপ্রিয় ২০টি ভুয়া নির্বাচনী সংবাদ মূলধারার ২০টি সত্য খবরের তুলনায় বেশি লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট পেয়েছিল। এই ভাইরাল ভুয়া খবরগুলোর বেশিরভাগই ছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে এবং হিলারি ক্লিনটনের বিরুদ্ধে—যেমন, “পোপ ট্রাম্পকে সমর্থন করেছেন”—যা পরে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ফলস্বরূপ, কোটি কোটি ভোটার এই ভুয়া তথ্য দেখেছেন এবং বিশ্লেষকদের মতে, এটি নির্বাচনী জনমতকে কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত করেছে।
উপরের উদাহরণগুলো থেকে এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, গণতন্ত্রে স্বচ্ছ ও স্বাধীন তথ্যপ্রবাহ ব্যাহত হলে ভুল তথ্য জনমতকে প্রভাবিত করে এবং ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। একবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে তথ্যনিয়ন্ত্রণ কঠিন হয়ে পড়েছে; ফলে মিথ্যা খবর দমন করতে আরও সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সচেতন নাগরিক ভাবনা এখনো দুর্বল কাঠামোয় রয়ে গেছে— বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর প্রকটতা আরও তীব্র।
উদাহরণস্বরূপ, ৫ আগস্ট ২০২৪ ক্ষমতাসীন সরকারের পতন ঘটে এবং ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু এর পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আরেক ধরনের মিথ্যা তথ্য প্রচারণা জোরদার হয়, যার লক্ষ্য ছিল নতুন সরকার ও উদ্ভূত পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করা। বাংলাদেশের ফ্যাক্ট-চেকিং প্ল্যাটফর্ম রিউমার স্ক্যানার এর এক বিশেষ প্রতিবেদনে দেখা যায়, ৫–১৩ আগস্টের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে (প্রধানত এক্স/ টুইটারে) অন্তত ৫০টি অ্যাকাউন্ট থেকে পরিকল্পিতভাবে গুজব ও ভুয়া তথ্য ছড়ানো হয়। এসব পোস্টে উগ্র সাম্প্রদায়িক ন্যারেটিভ ব্যবহার করে আওয়ামী লীগের পতনের পর দেশটিকে অশান্ত দেখানোর চেষ্টা করা হয়। এই পোস্টগুলো মিলিয়ে প্রায় ১.৫৪ কোটি বার দেখা হয়েছিল।
গবেষণায় উঠে এসেছে, এসব ভুয়া তথ্য ছড়ানো অ্যাকাউন্টের ৭২% ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান থেকে পরিচালিত হচ্ছিল এবং কিছু ভারতীয় মূলধারার গণমাধ্যমও বাংলাদেশ সম্পর্কিত মিথ্যা খবরে শামিল হয়। উদাহরণস্বরূপ, আগস্টে ভারতীয় কিছু মিডিয়া ভুলভাবে দাবি করে যে বাংলাদেশে পূর্বে নিষিদ্ধ কয়েকটি জঙ্গি সংগঠনের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা নাকি তুলে নেওয়া হয়েছে, যা পুরোপুরি মিথ্যা প্রমাণিত হয়। আবার সামাজিক মাধ্যমে প্রচারিত আরেকটি গুজবে বলা হয়— ড. ইউনুস নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন কিংবা তিনি দেশ ছেড়ে ফ্রান্সে পালিয়ে গেছেন, যা ছিল ভিত্তিহীন ভীতি সৃষ্টির কল্পকাহিনি। অর্থাৎ, বাংলাদেশের পরাজিত রাজনৈতিক শক্তির মদদপুষ্ট একটি সংঘবদ্ধ অপপ্রচার যন্ত্র নতুন সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে এবং জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তথ্যপ্রবাহের ওপর পূর্ববর্তী সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও গণমাধ্যমের ভীতিজনক পরিবেশের কারণে জনগণের একটি অংশ এমনিতেই অবিশ্বাসে ছিল; তার ওপর এই ধরনের মিথ্যা প্রচারণা সংকটকে আরও ঘনীভূত করেছে।
বাংলাদেশে এই সময়কালে রাষ্ট্রও নিজেদের পক্ষের “বর্ণনা” জনগণের কাছে পৌঁছাতে সচেষ্ট ছিল না। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের এক মন্ত্রীর বক্তব্য ছিল যে, সোশ্যাল মিডিয়াতে “রাষ্ট্রবিরোধী ভুল তথ্য” ছড়িয়ে সহিংসতা হয়েছে এবং সেটি নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরকার আরও কিছু পদক্ষেপ নেয়—যেমন, ২ আগস্ট থেকে কর্তৃপক্ষের অনানুষ্ঠানিক নির্দেশে মোবাইল নেটওয়ার্কে কিছু সোশ্যাল মিডিয়া সাইট বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ভিপিএন ব্যবহারের বিরুদ্ধে জনগণকে সতর্ক করা হয়। তবে বিশ্লেষকদের মতে, এতে সাধারণ মানুষ আরও অবিশ্বাস ও তথ্যসংকটে পড়ে, যার ফলে সরকার ও নাগরিকদের মধ্যকার দূরত্ব বেড়েছে এবং গুজব মোকাবিলাও কঠিন হয়ে পড়েছে।
বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা এবং বিশ্বপর্যায়ের উদাহরণগুলো একটি মৌলিক শিক্ষা দেয়: তথ্যপ্রবাহের স্বাধীনতা নিশ্চিত না থাকলে ও রাষ্ট্র কর্তৃক তথ্য নিয়ন্ত্রণ বাড়ালে সমাজে ভুয়া তথ্য, গুজব ও প্রোপাগান্ডার বিপজ্জনক বিস্তার ঘটে। যখন জনগণ বিশ্বাসযোগ্য ও নিরপেক্ষ তথ্য পায় না, তখন তারা সহজেই অসত্য সংবাদের শিকার হয়। সঠিক তথ্যের অভাব তাদের ভীত, বিভ্রান্ত বা উত্তেজিত করতে পারে, যার সুযোগ নেয় অসৎ রাজনৈতিক শক্তি ও বিভ্রান্তিকারীরা। ফলস্বরূপ, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সামাজিক অস্থিরতা বাড়ে এবং এমনকি সহিংস পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। ইতিহাস থেকে শুরু করে আধুনিক প্রযুক্তিযুগ— প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা এই বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করছি। তাই বলতে হয়, যেখানে তথ্য থেমে যায়, সেখানেই গুজব জন্ম নেয়।
শামসুল আরিফ ফাহিম
গবেষণা সহকারী, সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস)
Content Courtesy:
যেখানে তথ্য থেমে যায়, সেখানেই গুজব জন্ম নেয়: ভুয়া তথ্যের রাজনীতি ও বিপর্যয়ের বিবর্তন