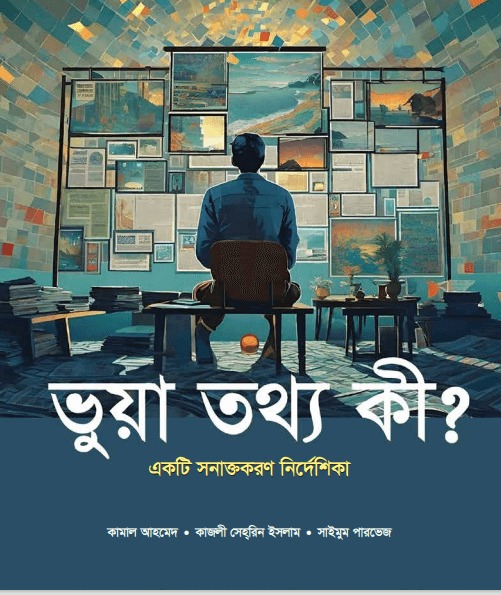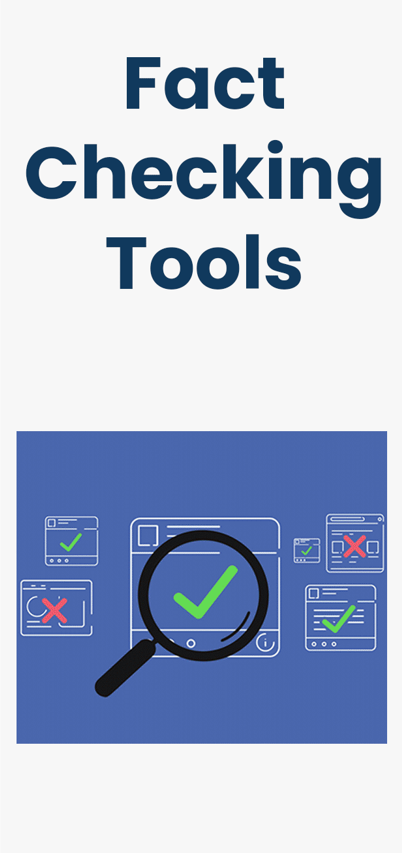নুজহাত তাবাসসুম
বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রুপান্তর করার জন্য বিগত সরকার গত এক দশক ধরে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। গত এক দশকে বাংলাদেশে ডিজিটাল রূপান্তরের গতি অভাবনীয় হারে বেড়েছে। মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহারের বিস্তার যেমন সুযোগের দরজা খুলে দিয়েছে, তেমনি খুলে দিয়েছে এক ভয়ঙ্কর ঝুঁকির। সেটি হলো—ভুয়া তথ্য বা মিথ্যা সংবাদ ছড়ানো। এই তথ্যবিকৃতি এখন কেবলমাত্র বিভ্রান্তি বা মিথ্যাচার নয়, বরং তা পরিণত হয়েছে জাতীয় নিরাপত্তা, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনের ওপর ভয়াবহ হুমকিতে। ভুয়া তথ্য ভয়ংকর রুপে দাঁড়াতে পারে তার দৃষ্টান্ত হল ২০১৯ সালে ভোলায় সহিংস সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে একটি ভুয়া ফেসবুক বার্তার কারণে। এর পরিণতিতে কমপক্ষে চারজন নিহত হন, শতাধিক মানুষ আহত হন, এবং একটি নাজুক সমাজ আরও বিভক্তির দিকে ঠেলে পড়ে। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ২০১২ সালে কক্সবাজারে বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস, ২০১৬ সালে নাসিরনগরে সহিংসতা, কিংবা ২০২১ সালে কুমিল্লায় দুর্গাপূজার সময় সংঘটিত হামলা—সব ঘটনায় দেখা যায় একই প্রবণতা। ভুল তথ্যের কারণে বাংলাদেশ বহুবার চরম মূল্য পরিশোধ করেছে। জুলাই বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে এই ভুয়া তথ্যের প্রচার আরও বেড়েছে। এবং এর পিছনে একটি নীতিহীন গোষ্ঠী প্রতিনিয়ত কাজ করে চলছে।
ভুয়া তথ্য সাধারণত উদ্দেশ্যমূলকভাবে ছড়ানো হয়—যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানকে হেয় করা হয়, বা জনমতকে ভুল পথে পরিচালিত করা হয়। বাংলাদেশে এটি এখন ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে। বিশেষ করে রাজনৈতিক উত্তাপ, ধর্মীয় উত্তেজনা, বা নির্বাচনকালীন সময়ে এই ভুয়া তথ্যগুলো এক ভয়াবহ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। একেকটি ফেসবুক পোস্ট, স্ক্রিনশট বা ভিডিওর মাধ্যমে পুরো একটি জনপদ উত্তাল হয়ে উঠছে, মানুষ হত্যা পর্যন্ত ঘটছে। রাজনৈতিক বিভাজনকে তীব্র করার জন্য এখন ভুয়া তথ্য এক অদৃশ্য অস্ত্রের মতো কাজ করছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া বিকৃত বক্তব্য, বিভ্রান্তিকর ছবি বা ভিডিওর মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে হেয় করা হচ্ছে, এবং একই সঙ্গে সাধারণ জনগণের মধ্যে ভুল বার্তা ছড়িয়ে উত্তেজনা তৈরি করা হচ্ছে। এটি রাজনৈতিক শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে নষ্ট করছে এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে হুমকির মুখে ফেলছে।
বাংলাদেশে ফেসবুক ব্যবহারকারী সংখ্যা বেশি। এমন সামাজিক মাধ্যমে কোন তথ্য আসলে পড়লে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষ সেই তথ্যের সত্যতা যাচাই না করেই তা বিশ্বাস করে ফেলে। এর ফলে জনমনে আতঙ্ক, ভয়, এমনকি কেউ এই ভুয়া তথ্যের উপর বিশ্বাস করে তার উপর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে যার ফলে হাতাহাতি বা মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ দেখা যায় ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর ক্ষেত্রে। ভুয়া তথ্য সমাজের ভেতরেও বিষ ঢেলে দিচ্ছে। বাংলাদেশে ভুয়া তথ্য ছড়ানোর প্রধান মাধ্যম হলো ফেসবুক, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ, এক্স (টুইটার) ও বিভিন্ন ব্লগপোর্টাল। ক্লিকবেইট শিরোনাম দিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়া, ডিপফেক ভিডিও তৈরি করা, পুরনো ভিডিওকে নতুন ঘটনা বলে চালানো—এসব এখন সাধারণ কৌশল। বিশেষ করে বট অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে এসব পোস্ট দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া হয়। একটি মিথ্যা পোস্ট কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লাখো মানুষের মধ্যে পৌঁছে যায়। বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ভুয়া তথ্যের প্রচার বেশি হয়ে থাকে। নির্বাচন, রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি, উপদেষ্টা এমনকি বৈদেশিক নেতাদেরকে নিয়েও ভুয়া তথ্য প্রচার হয়। যার ফলে জনগণ সঠিক রাজনৈতিক সিধান্ত নিতে পারে না। ধর্মীয় ভুয়া তথ্য আরও ভয়ংকর। এর ফলে আমদের মতো সমাজে যেখানে সহনশীলতা কম, ফলে সহজেই এটি সহিংসতায় রূপ নিতে পারে। এটি ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সমস্যায় পড়তে পারে। সম্প্রতি জুলাই বিপ্লবের পড়ে ভারতীয় কিছু মেটা অ্যাকাউন্ট বাংলাদেশকে নিয়ে ধর্মীয় নির্যাতনের ভুয়া তথ্য ছড়াচ্ছে। এতে বাংলাদেশের নাম বহির্বিশ্বে খারাপ হচ্ছে।
এই সমস্যার সমাধানে কেবল আইন নয়, প্রয়োজন বহুস্তরীয় সমন্বিত উদ্যোগ। প্রথমত, শিক্ষাব্যবস্থায় মিডিয়া লিটারেসি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিশু-কিশোর এবং সাধারণ মানুষরা যেন বুঝতে পারে কোন তথ্য সঠিক, কোনটা নয়—তা শেখাতে হবে প্রাথমিক থেকেই। দ্বিতীয়ত, স্বাধীন ফ্যাক্ট-চেকিং সংস্থাগুলোকে উৎসাহ দিতে হবে, যারা দ্রুত তথ্য যাচাই করে তা জনসাধারণকে জানাবে। রিউমার স্ক্যানার, ফ্যাক্ট ওয়াচ, আজকের পত্রিকাম ডিসমিস ল্যাব ইত্যাদি প্ল্যাটফর্মকে সরকারি ও সামাজিকভাবে সমর্থন করা দরকার। তৃতীয়ত, ফেসবুক, ইউটিউব-এর মতো সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলোকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে তাদের ভুয়া কনটেন্ট শনাক্তকরণ এবং রিমুভ করার প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ করে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দ্বারা তৈরিকৃত ভুয়া কন্টেন্ট প্রচারে বাঁধা, ফ্যাক্ট-চেকিং টুলস ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা উচিত। চতুর্থত, সাধারণ জনগণের মধ্যেও সচেতনতা বাড়াতে হবে। কেউ যদি ভুয়া বা সন্দেহজনক তথ্য দেখে সঙ্গে সঙ্গে তা রিপোর্ট করে, কিংবা ছড়িয়ে না দেয়—তাহলে এর বিস্তার অনেকাংশে ঠেকানো সম্ভব। এজন্য গোপন ও নিরাপদ রিপোর্টিং ব্যবস্থা থাকা জরুরি। পঞ্চমত, গণমাধ্যমগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় কিছু অনলাইন সংবাদপোর্টাল তথ্য যাচাই ছাড়া শুধুই ‘সেনসেশন’ তৈরি করতে গিয়ে বিভ্রান্তিকর খবর প্রকাশ করে। ‘কে আগে দেবে’—এই প্রতিযোগিতার চেয়ে ‘সঠিকভাবে কে দেবে’—এই মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে সাংবাদিকদের মাঝে। এর পাশাপাশি সরকারেরও উচিত আলাদা সরকারি উদ্যোগে একটি ফ্যাক্ট চেক সেল চালু করা।
তথ্য এখন কেবল জ্ঞানের উৎস নয়, এটি শক্তিও। কিন্তু এই শক্তি যখন মিথ্যার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তখন তা ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই এর ক্ষতিকর প্রভাবের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এখন সময় এসেছে সত্য ও দায়িত্বশীলতার পক্ষে দাঁড়ানোর। সরকার, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম এবং প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান—সবাইকে মিলে ভুয়া তথ্য মোকাবেলায় এগিয়ে আসতে হবে। না হলে ভবিষ্যতে এই তথ্য-সন্ত্রাস আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে, যখন ভুয়া তথ্য সমাজে বিভ্রান্তি ও সহিংসতা সৃষ্টি করছে, তখন তথ্য যাচাই কোনো বিলাসিতা নয়—বরং বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এটি একটি অপরিহার্য হাতিয়ার।
নুজহাত তাবাসসুম
প্রোগ্রাম অ্যাসিসট্যান্ট, সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস)
Content Courtesy: