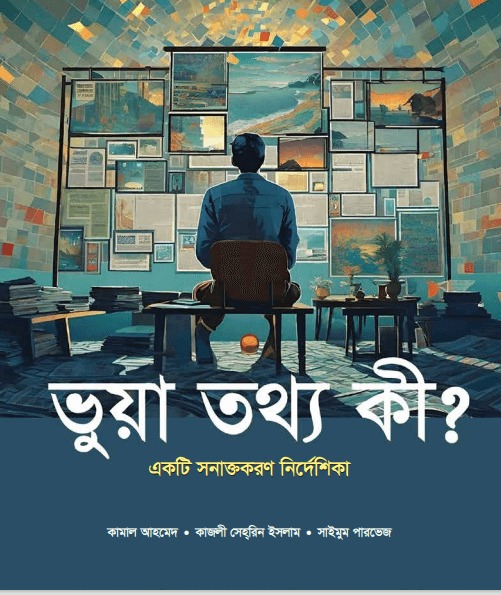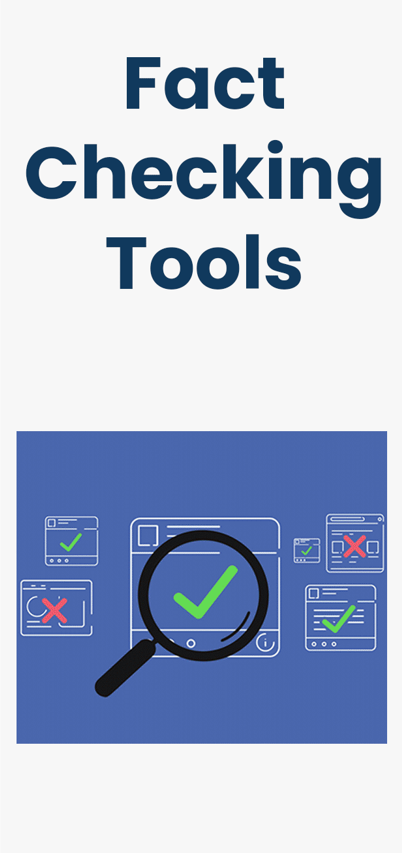সম্প্রতি ‘সোরা’ নামের একটি অ্যাপ ইন্টারনেট জগতে বেশ সারা সাড়া ফেলেছে। টিকটকের অনুকরণে এই অ্যাপটি বানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান “ওপেন এআই”। বর্তমানে বহুল জনপ্রিয় চ্যাট জিপিটিও প্রতিষ্ঠা করেছিল এ প্রতিষ্ঠানটি। ওপেন এআই-ই চ্যাট জিপিটির প্রস্তুতকারক কোম্পানি।
তাদের এই নতুন অ্যাপটি দেখতে প্রায় টিকটকের মতোই কিন্তু এখানে মানুষের তৈরি কোনো কন্টেন্ট নেই এবং প্রত্যেকটি ভিডিও-ই এআই দ্বারা তৈরি। অ্যাপটি ওপেন করার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মুখমন্ডলের একটি স্ক্যান নেয়, তার উপর ভিত্তি করে এই অ্যাপে আপনি প্রম্পট দেবেন, ‘লন্ডনের বিগ বেন ঘড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি ডাকছি’ আমাকে এরকম একটি ভিডিও দাও। সে আপনাকে সেরকম-ই একটা ভিডিও তৈরি করে দেবে, এবং সেটাই আপনার কন্টেন্ট। সেটাকে বদলাতে হলে ভিন্ন প্রম্পট দিয়ে বদলিয়ে আপনার মন মতো করে তারপর আপনি পোস্ট করতে পারবেন। নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে এর প্রস্তুতকারকরা এটার উপর পরিবর্তনশীল কিছু জলছাপ রাখার বাধ্যবাধকতা রেখেছেন।
একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কেউ যদি সেলফি তুলতে গিয়ে তাঁর মুখের স্ক্যান নিয়ে নেয়, সেটা দিয়ে সে যা ইচ্ছা বানাতে পারবে। অবশ্যই সেখানে জলছাপের মতো নিরাপত্তা বেষ্টনী আছে, কিন্তু ভয়টা শুধুমাত্র এইটুকু নিয়েই না। ভয় হচ্ছে এই প্রযুক্তির মাত্র শিশু অবস্থায় আমরা বাস করছি, ১৫-২০ বছর আগে ফেসবুক যেমনটা ছিলো, সময়ের সঙ্গে এই প্রযুক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
এআই এর বিভিন্ন ব্যবহার আমরা এখনই দেখতে শুরু করেছি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে। ডিপফেক এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত মাধ্যম ব্যবহার করে অপতথ্যের ছড়াছড়ি নিয়ে দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন গবেষণা হচ্ছে, রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে এটিকে শঙ্কাজনক অবস্থায় দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। ছোটবেলা থেকে প্রযুক্তির সঙ্গে বড় হওয়া মিলেনিয়াল বা জেন-জি যারা আগে কৃত্রিম থেকে বাস্তব ভিডিও বা ছবি আলাদা করতে পারতো তাঁরাও এখন হিমশিম খাচ্ছেন।
বিশেষত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা চলাকালীন ভুল বা সঠিক যাচাই করার আগেই মনস্তাত্ত্বিক ভাবে একটি পক্ষপাতিত্ব সৃষ্টি হয়, যা স্বাভাবিক মানবীয় আচরণ। ধরুন, একটা রাজনৈতিক অথবা সামাজিক অস্থিতিশীল সময় চলছে, হয়তো কোনো পলিসিগত একটি আলাপ অথবা নারী হেনস্তার একটি ঘটনা সমাজের বৃহত্তর মনস্তত্বে প্রভাব ফেলছে। সেই সময় এমন একটি কন্টেন্ট আপনার সামনে এসে হাজির হলো যেটি আপনার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করলো, আপনার অনুভূতিকে একটি নির্দিষ্ট দিকে ঠেলে দিলো, হয়তো কেউ নিছক মজা করে অথবা কোনো স্বার্থেই সেটা তৈরি করেছে। আপনি পরবর্তীতে জানতে পারলেন যে সেই কন্টেন্টটি ছিলো মিথ্যা বা ভুয়া, আপনি পরবর্তীতে যখন একটি সংকটময় মুহূর্তে সত্য কোনো তথ্য দেখবেন তারপরেও সেটাকে ভুয়া ভেবে এড়িয়ে যাবেন। যখন আপনার মতামত সমাজের সমষ্টিগত প্রতিক্রিয়ার একটি প্রয়োজনীয় বহিঃপ্রকাশ। সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন অসঙ্গতিপূর্ণ বিষয় যদি এআই অথবা ‘এগুলো এডিট করা যায়’ বলে চালিয়ে দেয়া যায় সেটা ভবিষ্যৎ জবাবদিহিতার জন্য অত্যন্ত বিপদজনক।
ভুয়া বা অপতথ্য সংক্রান্ত যেকোনো আলোচনায় একটি বিষয় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক যা হলো বট অ্যাকাউন্ট। এইসকল অপতথ্যের বিষয়বস্তুর উৎপত্তিস্থল এক নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার হলেও, বণ্টনের কৌশল সেই আগের মতোই আছে। একদিক থেকে কন্টেন্ট তৈরি হয়, বণ্টনের জন্য ব্যবহার হয় বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভুয়া বেনামী একাউন্ট। অনেক সময় একজন ব্যক্তি একাধিক একাউন্ট চালিয়ে এগুলো করে, আবার অনেক ক্ষেত্রে কোডিং করে একাধিক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হয়। শঙ্কার বিষয় হচ্ছে, ইম্প্রেভা সাইবার সিকিউরিটি নামের একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বলছে বর্তমানে ইন্টারনেটের ৫১% কন্টেন্ট-ই বট দ্বারা তৈরি অথবা বন্টিত হচ্ছে। অর্থাৎ এটি যে শুধুমাত্র বাংলাদেশের সমস্যা তা নয়, সমস্যাটি বৈশ্বিক। এই ৫১% এর ভেতর ৩৭% কে ইম্প্রেভা চরিত্রায়ন করেছে খারাপ বট হিসাবে এবং ১৪% ভালো বট হিসাবে। এই চরিত্রায়নে তাঁরা যাদের ভালো বট বলছে তাঁরা মূলত সার্চ ইঞ্জিনের ইন্ডেক্সিং করে ক্ষতিকারক কন্টেন্টকে চিহ্নিত করে। সুতরাং শুধুমাত্র সংখ্যা বা গড় হিসাব করলে খারাপ বটের সংখ্যা-ই বেশি।
এই অপতথ্য বা ভুয়া তথ্য যে শুধুমাত্র সামাজিক, রাজনৈতিক বয়ানে প্রভাব ফেলছে তা-ই নয়। বরং শিশুদের মস্তিষ্কের পরিপক্কতায়-ও বড় ধরনের একটি প্রভাব ফেলছে বলে মনোবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞরা বলছেন। একজন মানুষের মস্তিষ্কের প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স পুরোপুরি পরিপক্ক হতে সময় লাগে তার জীবনের প্রথম ২৫ বছর, এই সময়টাতে তাঁর মনোযোগ ক্ষমতা এবং শেখার ক্ষমতা থাকে সবচাইতে বেশি। এই বয়সটাতে যদি এই ধরণের কন্টেন্ট একজন প্রতিনিয়ত দেখতে থাকে, তাঁর মস্তিস্কের যেই জ্ঞানের চাহিদা তা যদি অপতথ্য দ্বারা পূর্ণ হয়, তবে সে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠবেনা। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের সঙ্গে সমঝোতায় আসার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু একজন শিশু বা কিশোরের সঙ্গে সমঝোতায় এসে তাঁকে বোঝানোটা বিশাল কঠিন একটি কাজ।
যখন ডট-কম যুগে আমরা প্রবেশ করি, মুক্ত তথ্য তথা ইন্টারনেট কে আমরা একটি আশীর্বাদ হিসাবে দেখেছিলাম। সেই মুক্ত তথ্যকে পুঁজি করে তৈরি হয় ইনফরমেশন ইকোনমি বা তথ্য অর্থনীতি, যেই অর্থনীতির সিঁড়ি বেয়ে বড় হয়ে ওঠে ফেসবুক, গুগল, ইউটিউবসহ বিভিন্ন কোম্পানি। আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য বিক্রি করে আমাদেরকে তৈরি করা হয় পণ্যে। এই সমস্যার সমাধান তো দূরে থাক, সমস্যা নির্ণয় করার আগেই আমাদের এই অপতথ্যের যুগে প্রবেশ করতে হলো।
এই সমস্যাটাকে ব্যক্তিগতভাবে আমি দেখি অপতথ্য অর্থনীতি, অথবা মিসইনফরমেশন ইকোনমি হিসাবে। বর্তমানে অপতথ্য ছড়ানো অথবা তৈরি করার মধ্য দিয়ে এক ধরণের বাজার তৈরি হয়েছে। ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম এখন তাদের ব্যবহারকারীদের কয়েক হাজার ফলোয়ার হলেই উৎসাহিত করে ‘ডিজিটাল ক্রিয়েটর’ হওয়ার জন্য, কোম্পানীর পর্বত-সমান মুনাফার কিছু ছিটেফোঁটা বালুকণা এইসকল তথাকথিত ডিজিটাল ক্রিয়েটরদের দেয়। এই এক দুই ডলারের প্রলোভনে বহু মানুষ এআই এর সাহায্য নিয়ে অথবা বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহলের প্রণোদনায় কন্টেন্ট বানায়। এইসকল ব্যক্তিবর্গ সামাজিক অথবা রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন না। যৎসামান্য ব্যক্তিগত অর্থ অর্জন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চাকচিক্য সম্পন্ন জনপ্রিয়তার ঘোমটা তাদেরকে এক ধরণের অনুপ্রেরণা দেয়।
বর্তমানেই এই দশা হলে ভবিষ্যৎকে খুব একটি আশা নিয়ে দেখার জায়গা নেই, ইন্টারনেটের শুরুর দিকে যেটা ছিলো। সকলের কাছে তথ্য পৌঁছাতে পারলেই যে তাঁদেরকে শিক্ষিত করা যায়না সেটার সবচাইতে বড় উদাহরণ হচ্ছে গত দুই দশক, কারণ বিশ্বের একটা বড় অংশের কাছে আমরা জ্ঞান অর্জনের যন্ত্রটি দিতে পেরেছি ঠিকই কিন্তু জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছাটি সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছি।
এই অবস্থায় আমাদের করণীয় কী? কী করে আমরা এই অপতথ্য অর্থনীতির মায়াজাল থেকে বের হয়ে আসতে পারি? নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কর্তা-ব্যক্তিরা আদৌ কী এসকল সমস্যা নিয়ে ভাবছেন কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে, সুতরাং আমাদের ব্যক্তিগত জায়গা থেকে যতোটুকু করার সেটুকুই করতে হবে। ২৫ বছরের কম বয়সী শিশুকিশোরদের যতোটুকু সম্ভব বোঝাতে হবে, তবে জোর করা যাবেনা, কারণ নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বরাবর-ই বেশি থাকে। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে, যেই তথ্য নেতিবাচক অনুভূতির উদ্রেক ঘটায় সেই তথ্য অন্যদের জানানোর আগে নিজে যাচাই করার চেষ্টা করতে হবে। আশেপাশের কেউ যদি এই ধরণের তথ্য ছড়ায় তখন তার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে যে এই তথ্যটির সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা কতোটুকু। নিজের ক্ষেত্রে নিতান্তই চোখে দেখা ঘটনা ছাড়া অন্য কিছুকেই বিশ্বাস করার আগে কয়েকবার ভাবতে হবে। নিজের চোখে দেখার কথা দিয়ে এই লেখাটির ইতি টানতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়লো ‘মেটা’ এক ধরণের সাশ্রয়ী ‘স্মার্ট গ্লাসেস’ বের করছে, যা দিয়ে আপনার চোখেও যা ইচ্ছা তা দেখানো সম্ভব।
News Courtesy:
তথ্যের স্বাধীনতা থেকে অপতথ্যের খাঁচায়